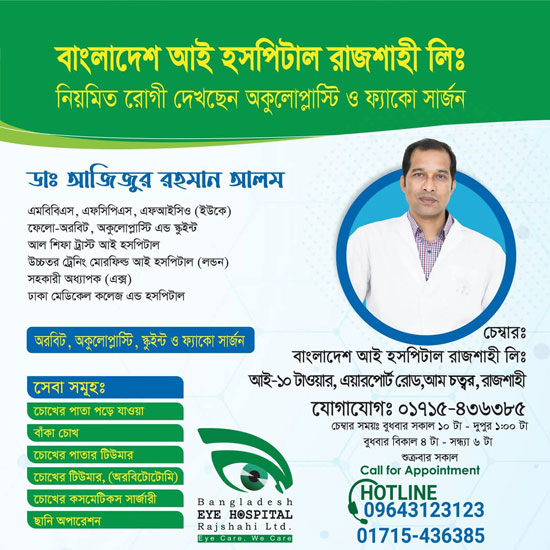সোনার বাংলা গঠনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা
পদ্মাটাইমস ডেস্ক : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের বন্দিদশা থেকে মুক্তি পান ১৯৭২ সালের প্রথম সপ্তাহে। এরপর অনবদ্য এব সংবর্ধনার মাধ্যমে সদ্য স্বাধীন দেশের রাজধানী ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন একই বছরের ১০ জানুয়ারি। পথে তিনি যাত্রা বিরতি দেন লন্ডন ও নয়াদিল্লি।
বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য একজন সম্মোহনী নেতা এবং জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী বঙ্গবন্ধু ব্যাপক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি নয়াদিল্লির পালাম বিমানবন্দরে নতুন দেশ নিয়ে তাঁর ভিশনের কথা বলেন। বাংলাদেশকে মুক্ত করাকে তিনি সেদিন বর্ণনা করেন ‘বন্দিদশা থেকে স্বাধীনতা, নিরাশা থেকে আশার’ যাত্রা হিসেবে। সেদিন আরো বলেন, তিনি স্বাধীন দেশে ফিরছেন হূদয়ে কারো প্রতি কোনো ঘৃণা নিয়ে নয়। বরং তিনি ফিরছেন পরম সন্তুষ্টি নিয়ে যে, অবশেষে মিথ্যার বিপরীতে সত্য, উন্মত্ততার বিপরীতে সুবিবেচনা, কাপুরুষতার বিপরীতে সাহস, অন্যায়ের বিপরীতে ন্যায় এবং মন্দের বিপরীতে ভালোর জয় হয়েছে।
একজন রাষ্ট্রনায়ক, অবিশ্বাস্য বাগ্মী বঙ্গবন্ধু খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রথমবারের মতো স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে পা রেখেই আবেগে বিপুলভাবে অভিভূত হয়েছিলেন। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ১০ জানুয়ারি দেয়া ভাষণে তিনি খুব দক্ষতার সঙ্গে বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপের কথা বলেন এবং বাংলাদেশের বিজয়ী জনগণের উদ্দেশে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেন। প্রথম সুযোগেই তিনি কাউকে অবাঙালিদের ওপর হাত না তুলতে সতর্ক করেন। একই সঙ্গে পাকিস্তানে আটকা পড়া চার লাখ বাঙালির নিরাপত্তার বিষয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন। সাধারণ পাকিস্তানিদের প্রতি তাঁর কোনো বিদ্বেষ নেই, এটা যেমন নিশ্চিত করেছেন, তেমনি পরিষ্কার করে বলেছেন, অন্যায়ভাবে বাঙালিদের যারা হত্যা করেছে, তাদের অবশ্যই বিচারের মুখোমুখি হতে হবে।
একই ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ এক বিবৃতিতে মুসলিম বিশ্বের উদ্দেশে তিনি বলেছেন, কেবল ইন্দোনেশিয়ার পরেই বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র (বাংলাদেশে ইসলামের প্রতি বিশ্বাস বিপন্ন— পাকিস্তানিদের এমন প্রচারণার জবাবে তিনি এটা বলেছেন)।
তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে তিনি আরো বলেন, ‘ইসলামের নামে এ দেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী মুসলমানদের মেরেছে, অসম্মান করেছে নারীদের। আমি ইসলামকে অসম্মান করতে দিতে চাই না।’
তিনি তদন্তের জন্য একটি আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল গঠন এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশে চালানো গণহত্যার পরিসর নির্ধারণের আহ্বানও জানান জাতিসংঘকে।
উল্লিখিত, মতামতগুলো আন্তঃসম্পর্কিত এবং সেসবে কেবল যুদ্ধাপরাধের বিচারের ব্যাপারে তাঁর দৃঢ় অঙ্গীকারই প্রকাশ পায়নি; উপরন্তু প্রকাশ পেয়েছে ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তান কর্তৃক ইসলামের অপব্যবহারের বিষয়টিও। এই একই দৃষ্টিভঙ্গিই তাকে পরিচালিত করেছিল ১৯৭২ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি ওআইসির ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করতে। তখনকার ওআইসির মহাসচিব টেঙ্কু আবদুর রহমানকে তিনি বলেছিলেন, দ্বিতীয় মুসলিম দেশ হওয়া সত্ত্বেও (১৯৭১ সালে) নয় মাসে পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ঠাণ্ডা মাথায় নিরাপরাধ মুসলিম ও অন্য সম্প্রদায়ের মানুষকে খুন করলে তার বিরুদ্ধে ওআইসি কোনো প্রতিবাদ করেনি। ওআইসি মহাসচিব এর পাল্টা জবাব হিসেবে পরে বাংলাদেশে বসবাসরত বিহারি ও অন্য অবাঙালি মুসলিমদের প্রতি বাঙালিদের আচরণে ক্ষুব্ধভাবে উদ্বেগ জানিয়েছিলেন।
পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী এবং তাদের সহযোগী কর্তৃক সংঘটিত অপরাধের তদন্ত সম্পন্ন হওয়ার পর ১৯৭৩ সালের ১৭ এপ্রিল গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ, জেনেভা কনভেনশনের ৩নং ধারা লঙ্ঘন, খুন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি মানবতাবিরোধী অপরাধে ১৯৫ জনকে বিচারের আওতায় আনার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আরো সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, এসব ব্যক্তি ও অপরাধ সংঘটনের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে জড়িত অন্য সহযোগীদের বিচার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিচারিক রীতি অনুযায়ী সম্পন্ন করা হবে। এ যুক্তি এবং সংশ্লিষ্ট বিচারিক প্রক্রিয়া ১৯৭৫ সালের নৃশংস আগস্ট হত্যাকাণ্ডের আগ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যু পুরো বিচারিক প্রক্রিয়াকে লক্ষ্যচ্যুত করে।
তবে এখন সৌভাগ্য যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মানবতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধের বিচার প্রক্রিয়া কার্যকর হয়েছে এবং এখন সেটি প্রায় শেষ হতে চলেছে। আমরা এজন্য আজীবন ঋণী থাকব লাখ লাখ মানুষের কাছে, যারা নিজেদের পরিবার হারিয়েছে এবং ১০ হাজার নারী, যারা নিগ্রহের শিকার হয়েছিলেন।
পরবর্তীতে দৃঢ় অবস্থান সত্ত্বেও ১৯৭৩ সালের মিসর-ইসরায়েল যুদ্ধের সময় বঙ্গবন্ধু ইসলাম, আরব দেশ এবং ওআইসিকে সমর্থনে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠতা দেখাতে দ্বিধা করেননি। তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগেই তখন মিসর ও সিরিয়ায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চিকিৎসক দল ও চায়ের কার্টুন পাঠানো হয়েছিল। ওআইসির সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক এটা ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছিল এবং এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে লাহোরে অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনে সংস্থাটির পক্ষ থেকে বাংলাদেশকে সদস্য হওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হয়।
বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সরকারের অন্য গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হলো, বিধ্বস্ত দেশের যুদ্ধাক্রান্ত নাগরিক এবং ভারতের সীমান্তে আশ্রয় চাওয়া ১০ মিলিয়নের অধিক শরণার্থীর মধ্যে আস্থা সৃষ্টি করা। ১৯৭২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কলকাতায় বলেছেন যে, ছয় সপ্তাহের স্বল্পসময়ে সাত মিলিয়নের অধিক শরণার্থীকে ভারত থেকে বাংলাদেশে ফিরে আসতে হবে। যথারীতি সেটা করা হয়েছে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক হাজার হাজার নির্যাতনের শিকার হওয়া মানুষগুলো সেখান থেকে দেশে ফিরে এসেছে। তাদের নতুন জীবন শুরু হয়েছে। এ রকম বিপুল জনসংখ্যার ত্রাণ ও পুনর্বাসন নিঃসন্দেহে দুঃসাহসিক কাজ। তবে জাতিসংঘের সহযোগিতায় এ দুঃসাহসিক কাজই দক্ষতার সঙ্গে মোকাবেলা করেছেন বঙ্গবন্ধু ও তাঁর দল।
সুনির্দিষ্টভাবে পররাষ্ট্রনীতিতে বঙ্গবন্ধুর গভীর আগ্রহ ছিল। তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে কেবল বাংলাদেশের প্রতি অন্য দেশের স্বীকৃতি আদায় ও কূটনৈতিক সম্পর্ক তৈরি নয়, উপরন্তু বাংলাদেশকে গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোয় সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তকরণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে উৎসাহিত করতেন। তাঁর নিজের বিদেশ সফর বা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বিদেশ সফরের প্রতিটি সুযোগে নির্দেশনা থাকত বাংলাদেশ যেন প্রত্যেকের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বমূলক ও ভালো প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক রাখে। তিনি জোটনিরপেক্ষ, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, পারস্পরিক সহযোগিতা, কারো অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা এবং ভূখণ্ডগত অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধার মতো মৌলিক নীতির ওপর বেশি জোর দিতেন।
বাঙালির মূলনীতি, প্রথা-রীতি ও জাতীয়তাবাদসহ বাংলাদেশের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক ঐতিহ্যের প্রতিও তিনি দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। সোনার বাংলায় বাঙালি হিসেবে বাস করা ছিল তাঁর গর্বের বিষয়। তিনি ছিলেন দেশের জন্য জীবন উৎসর্গকারী।