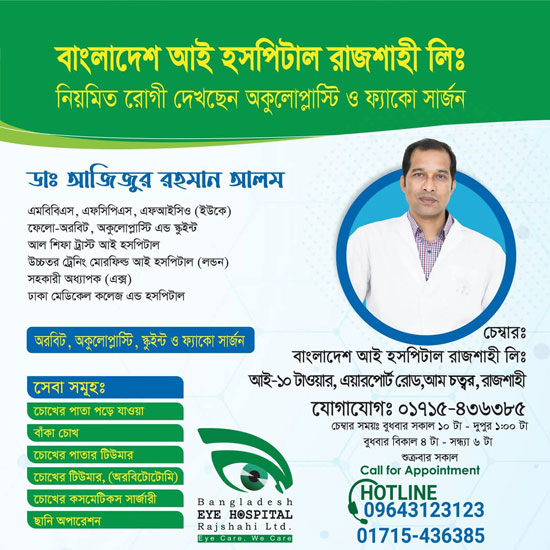বঙ্গের আদি পর্বের গান
গোলাম মুরশিদ : গলা ছেড়ে গান গাওয়া অথবা গুনগুন করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। সব সমাজেই মানুষ গান করে। যেসব ধর্মে সংগীত নিষিদ্ধ, সেসব ধর্মের লোকেরাও সুর করে ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ করে। কাজেই বলতে হয়, প্রাচীন বঙ্গভূমির বিভিন্ন অঞ্চলের আদিবাসীরাও গান গাইতো, তবে বাংলা ভাষায় নয়। কারণ চর্যাপদের ভাষাই তখনো পুরোপুরি বাংলা হয়ে ওঠেনি। তার আগেকার ভাষা তো নয়ই। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীগুলো গান গাইতো তাদের নিজের নিজের ভাষায় গান। এমন কি, সেই লোকসংগীতের সূত্র ধরে পরবর্তী কালের লোকসংগীত রচিত হয়েছিলো। কিন্তু সেসব গান বহু আগেই লোপ পেয়েছে।
তখনকার আদিবাসীদের বাদ্যযন্ত্রও পরবর্তী কালে রক্ষা পেয়েছে কিনা, জানা যায় না। ধরে নেওয়া যায় যে, তারা অনুন্নত ধরনের কোনো বাঁশি বাজাতো। সে বাঁশির গায়ে আঙুল দিয়ে বায়ুপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করার ছিদ্র থাকতো কিনা, জানি না। একতারা, কি দোতারার মতো কোনো তারযন্ত্র ছিলো কিনা, তাও অনুমানের বিষয়। আদিবাসীদের তালযন্ত্র নিশ্চয়ই ছিলো। তবে সে বাদ্যযন্ত্র হয়তো আধুনিক কালের ঢাক-ঢোলের মতো চামড়া দিয়ে ঢাকা ছিলো না। ছিলো অনুন্নত ধরনের ঢাক, ঢোল, মৃদঙ্গ, মাদল।
আদিবাসীদের তুলনায় বহিরাগত আর্যদের সভ্যতা ছিলো অনেক উন্নত। কিন্তু তারাও কী ধরনের গান এবং বাদ্যযন্ত্র নিয়ে এ অঞ্চলে এসেছিলো, তা জানা নেই। তাদের সামবেদ খ্রিস্টপূর্ব আমলের রচনা। দাবি করা হয় যে, তাতে সাতটি স্বর এবং একুশটি শ্রুতির বিবরণ আছে। সাতটি স্বরের বিকাশ ঘটে থাকলে, রাগরাগিণীও নিশ্চয় সৃষ্টি হয়েছিলো। তবে তখনকার রাগরাগিণীর কোনো পরিচয় জানা যায় না। সামবেদে বীণা জাতীয় বাদ্যযন্ত্রের কথা আছে। কিন্তু সে বীণা বঙ্গদেশ পর্যন্ত এসেছিলো কি? তা ছাড়া, ছিদ্রযুক্ত বাঁশির কথা জানা যায়, যাতে সাতটা স্বর বাজানো যেতো। আগেই বলেছি, সিন্ধুনদের অববাহিকায় অনার্যদের যে-সভ্যতা আর্যদের আগমনের আগেই গড়ে উঠেছিলো, প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে সেখান থেকে পোড়ামাটির বাঁশি ও ঢাক পাওয়া গেছে। তার অর্থ, ভারতবর্ষে বাঁশি ছিলো আর্য-পূর্ববর্তী বাদ্যযন্ত্র।

আর্যরা সুদূর বঙ্গদেশে যে- সংগীত নিয়ে এসেছিলো, তার খানিকটা রক্ষা পেয়েছে গুরুপরম্পরার মধ্য দিয়ে— চর্যাপদ থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আগেই বলেছি, প্রতিটি চর্যার ওপর রাগরাগিণীর নাম লেখা আছে। তবে রাগরাগিণীগুলোর সংখ্যা খুব বেশি নয়— মোট উনিশ। গবড়া আর গউড়া, এবং শীবরী আর শবরী এক হয়ে থাকলে, এগুলোর সংখ্যা উনিশ নয়, সতেরো। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক পদে যে-রাগিণীটি ব্যবহৃত হয়েছে, তার নাম পটমঞ্জরী। অন্য যেসব রাগিণীর নাম দেখা যায়, তার মধ্যে আছে গউড়া (গৌড়?), মালসী, মল্লারী, রামক্রী, কামোদ, বরাড়ী এবং বঙ্গাল। এই রাগিণীগুলোর কয়েকটি এখন লোপ পেয়েছে। এখনকার শাস্ত্রীয় সংগীতেও তাদের কোনো অস্তিত্ব নেই।
সে যাই হোক, চর্যাপদ যেমন বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন, তেমনি বাংলা গানেরও আদি নিদর্শন। এই পদগুলো রচনা করেছিলেন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা। হয়তো তাঁরা এগুলো গাইতেন সুর করে। রাগরাগিণীর উল্লেখ থেকে বোঝা যায় যে, তাঁরা নিজেরা শাস্ত্রীয় সংগীত জানতেন। কিন্তু তাঁদের শিষ্যরা সবাই সঙ্গীতশাস্ত্র শিখে সেই গানগুলো গাইতেন, তা মনে করা ঠিক হবে না। এমন কি, বেশির ভাগ লোক এ গানগুলো গাইতোও না সঠিক সুরে; বরং এক রকমের একঘেয়ে সুরে ঐ পদগুলো আবৃত্তি করতো— এখনো যেমন সবাই ধর্মগ্রন্থ এক রকম সুর করে আবৃত্তি করে – সে রকম। ধর্মের সঙ্গে মানুষের গভীর আবেগের যোগ আছে। তাই ধর্মীয় শ্লোক সুর করে আবৃত্তি করার রীতি সব ধর্মেই কমবেশি লক্ষ করা যায়। এমন কি সঙ্গীত-বিরোধী ইসলাম ধর্মেও। ব্স্তুত, বাংলা গানের সঙ্গে বঙ্গদেশে বিভিন্ন ধর্মের উত্থান-পতনের ইতিহাস অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে।
এখনকার মতো অতীতেও শাস্ত্রীয় সংগীতের চর্চা সীমাবদ্ধ ছিলো সমাজের অতিক্ষুদ্র একটি অংশে। তা সত্ত্বেও, সাধারণ মানুষ সে গান শুনতো। কেউ কেউ হয়তো গাইতেও চেষ্টা করতো। তা ছাড়া, মানুষ গান জানুক অথবা না-ই জানুক, সে মনের আনন্দে গান গায়। তবে গোটা সমাজে একই ধরনের গানের প্রতি আগ্রহ থাকে না। যেমন, গ্রামাঞ্চলে পল্লীগীতির সমাদর বেশি; শহরে আধুনিক গানের। শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে যেমন সামাজিক শ্রেণীর যোগাযোগ থাকে, গানের সঙ্গেও সামাজিক শ্রেণীর ঘনিষ্ঠ যোগে আছে।
চর্যাপদ বৌদ্ধদের, কিন্তু যারা বৌদ্ধ নয়, তারাও সেকালে তাদের ধর্মীয় সঙ্গীত রচনা করতো। যেমন, লক্ষ্মণসেনের দরবারে তখনকার সবচেয়ে বড়ো কবি ছিলেন জয়দেব। তিনি রচনা করেছিলেন ‘গীতগোবিন্দ’। নাম থেকেই দেখা যায়, এটি কাব্য নয়— এটি ছিলো গীত— রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা নিয়ে একটি পালাগান বা গীতিনাট্য। এতে গানগুলোই সংলাপের জায়গা করে নিয়েছে। গীতগোবিন্দের ভাষা বাংলা নয়, সংস্কৃত। তবে এই সংস্কৃত ভাষা অনেকটা বিদ্যাসাগর কিংবা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার কাছাকাছি। সমাস আর সন্ধি বিচ্ছেদ করলে বাংলার মতোই মনে হয়। গীতগোবিন্দকে তাই বঙ্গদেশেরই গান বলা যায়।
চর্যাপদের মতো, গীতগোবিন্দেও প্রতিটি গানের ওপর রাগরাগিণীর নাম দেওয়া আছে। এতে সর্বভারতীয় রাগরাগিণীর ব্যবহার চর্যাপদের চেয়ে বেশি। এই রাগিণীগুলোর প্রায় সবগুলোই এখনো প্রচলিত আছে। তবে গীতগোবিন্দে বেশি রাগিণী ব্যবহৃত হয়নি। বারোটি সর্গে রাগরাগিণীর সংখ্যা মাত্র বারোটি। প্রতিটি পদে তালের নামও লেখা আছে। যদিও তালের সংখ্যা মাত্র পাঁচ। এগুলো হলো: একতাল, অষ্টতাল, যতি, রূপক ও নিঃসার। চর্যাপদের সঙ্গে গীতগোবিন্দের চারটি রাগিণীর মিল আছে— গুর্জরী (গুঞ্জরী), দেশাখ, বরাড়ী এবং ভৈরবী। এতে যেসব রাগিণীর উল্লেখ আছে, তার মধ্যে একটি হলো মালবগৌড়। এ নাম থেকে মনে হয়, এও ছিলো উত্তর ভারত থেকে আসা মালব রাগিণীর বঙ্গীয় সংস্করণ।
বাংলা গানের ইতিহাসে এর পরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল হলো: বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। এটি রচিত হয়েছিলো গীতগোবিন্দের আড়াই শো/তিন শো বছর পরে। বর্তমান কালের ভাষায় এটি ছিলো একটি ‘মিউজিকেল’ অথবা গীতিনাট্য। রাধা, কৃষ্ণ আর বড়ায়ির সংলাপ পালাগানের আকারে লেখা। কাব্য-পরিকল্পনায় গীতগোবিন্দের সঙ্গে বেশ খানিকটা মিল আছে। গীতগোবিন্দে আছে বারোটি সর্গ। বড়ু চণ্ডীদাস সর্গকে বলেছেন খণ্ড। কিন্তু তাঁর কাব্যে খণ্ড বারোটিই। সাজিয়েছেন জয়দেবের মতো।
বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম গীতিনাট্য হওয়া সত্ত্বেও, বৈষ্ণব সমাজে এ কাব্যের খুব সমাদর হয়নি। কারণ এ কাব্যের বিষয়বস্তু রাধা-কৃষ্ণের দেহঘন প্রেম। চৈতন্যদেব প্রচারিত বৈষ্ণব-দর্শনের সঙ্গে এই প্রেমের সংগতি নেই। বৈষ্ণব দর্শনে রাধা জীবাত্মার প্রতীক, কৃষ্ণ পরমাত্মার। রাধার মিলন সেখানে কৃষ্ণকে আনন্দ দেবার জন্যে। ‘কৃষ্ণ ইন্দ্রেয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।’ তা সত্ত্বেও, বাংলা গানের ইতিহাসে এ কাব্যের গুরুত্ব খুব বেশি।
এতে রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে। কেবল তাই নয়, এর মধ্যে চর্যাপদ এবং গীতগোবিন্দের অব্যাহত সাংগীতিক ধারাও লক্ষ করা যায়। যেমন, রাগরাগিণীর মধ্যে চর্যাপদের গুর্জরী, বরাড়ি, দেশাখ(গ), ভৈরবী, পটমঞ্জরী, মল্লার, ভাটিয়ালি এবং বঙ্গাল শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ব্যবহৃত হয়েছে। কয়েকটা আবার গীতগোবিন্দের সঙ্গে অভিন্ন। এ ছাড়া, আলাদাভাবে গীতগোবিন্দের সঙ্গে মিল দেখা যায় মালব, দেশবরাড়ী, রামকিরি, বসন্ত ও বিভাস রাগিণীর। আগেকার রাগরাগিণীর সঙ্গে এই মিল ছাড়াও, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কেদার, কোড়া, ধানুষী, আহের (আহীর), ললিত, গৌরী, শ্রী, পাহাড়ী এবং বেলাবলী-সহ কিছু সংযোজন দেখা যায়। এই গীতিনাট্যে ৪১৮টি পদে মোট ৩২টি রাগরাগিণী ব্যবহৃত হয়েছে। দেখে মনে হয়, সংগীতে বড়ু চণ্ডীদাসের গভীর জ্ঞান ছিলো। আপাতদৃষ্টিতে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় রাগিণী ছিলো পাহাড়ী। এই সুরে তিনি ৫৭টি পদ রচনা করেছিলেন। তার পরই তাঁর প্রিয় রাগিণী ছিলো রামগিরি। এই রাগিণীতে গান বেঁধেছেন ৫৪টি। গুর্জরীতে আছে ৩৯টি গান। ভাটিয়ালিতে ১৭টি। একটি নতুন রাগিণীর নাম পাওয়া যায় বঙ্গালবরাড়ি।
বস্তুত, বঙ্গদেশে রাগরাগিণী চর্চার ইতিহাসে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন একটি অমূল্য নিদর্শন। একদিকে, এই পালাগান থেকে দেখা যায় যে, পনেরো শতকের শেষ নাগাদ বঙ্গদেশে রাগ-সংগীত চর্চার মান ছিলো বেশ উঁচু। অন্যদিকে, এ পালাগান থেকে আরও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, রাঢ় এবং উত্তরবঙ্গে রাগ-সংগীতের বেশ চর্চা হতো। কিন্তু পরবর্তী দু শো বছরের সংগীতে শাস্ত্রীয় প্রভাব এতোটা ছিলো কিনা বোঝা যায় না। কারণ পরে দেখা যাবে, শাস্ত্রীয় সংগীত ততোদিনে একটা বঙ্গজ চেহারা লাভ করেছিলো। চর্যাপদ, গীতগোবিন্দ এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বঙ্গদেশের পূর্বাঞ্চলে সংগীত চর্চার কোনো ইঙ্গিত দেয় না। তার স্বাক্ষর মেলে সতেরো শতকের কবি আলাওলের রচনা থেকে।
আলাওল জন্মেছিলেন পূর্ববঙ্গে, চ্ট্টগ্রাম অথবা ফরিদপুরে। কিন্তু যৌবনকাল থেকে তাঁকে দেখতে পাই মিয়ানমারের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে – রোসাং রাজদরবারে। (রোসাং শব্দ থেকেই রোহিংগা কথাটির উৎপত্তি।) জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি সেখানেই বাস করেন এবং সেখানে বসেই ‘পদ্মাবতী’-সহ বেশ কয়েকটি কাব্য রচনা করেন। প্রতিটি কাব্যেই সুর করে গাইবার অনেকগুলো পদ আছে। পদগুলোর ওপরে রাগরাগিণী এবং তালের নাম লেখা আছে। তবে এই সুরে পদগুলো গাওয়া হতো, নাকি ঐ পদগুলোর জন্যে এই সুরগুলো প্রযোজ্য– এটা বোঝা যায় না।
কোনো কোনো পদে তালের বদলে লেখা আছে ছন্দের নাম। সুরের সঙ্গে তালই যায়, ছন্দ নয়। অথচ আলাওল তালের নাম না-লিখে ছন্দের নাম লিখেছেন। এই রহস্য ভেদ করতে পারিনি। কিন্তু আলাওল যে গান ভালো জানতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি কয়েকটি রাগরাগিণীর ‘রূপ’ বর্ণনা করে কবিতা লিখেছেন। তাঁর আগে বাংলা ভাষায় এ কাজ অন্য কেউ করেননি।
গীতগোবিন্দ, চর্যাপদ এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নেই, অথচ আলাওলের রচনায় আছে— এমন অনেকগুলো রাগরাগিণীর নাম পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে আছে: আশাবরী, কল্যাণ, কাফি, টোরি, টোরি-বসন্ত, দক্ষিণী-শ্রী, ভূপালী, মঞ্জরী, মালশী, লাচারী, শ্রীরাগ-গান্ধার, সাহানা, সিন্ধুরা, সুহী, সুহী-পাহাড়ী। কেবল নতুন রাগরাগিণীর কথা নয়, আলাওলের রচনা থেকে রাগরাগিণীর সম্ভাব্য মিশ্রণের কথাও জানা যায়।
মোট কথা, পনেরো শতকের আগেই বঙ্গদেশে এবং বাংলা ভাষায় শাস্ত্রীয় সংগীত বেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো – শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকে তা পরিষ্কার দেখা যায়। যা দেখা যায় না, তা হলো, এর পাশাপাশি লোকসংগীত কতোটা বিকাশ লাভ করেছিলো। ভাটিয়ালি রাগিণীর কথা চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এবং আলাওলে আছে। এক হাজার বছর পরে এখনো ভাটিয়ালি একটি বিশেষ ধরনের লোকসংগীত। এ থেকে মনে হয় ভাটিয়ালী নামে এক রকমের লোকসংগীত বঙ্গে অর্থাৎ দক্ষিণ বঙ্গে আগে থেকেই প্রচলিত ছিলো। তারপর এই সুরের উপর ভিত্তি করে সঙ্গীতজ্ঞরা একে একটা রাগিণীর রূপ দান করেন। তাঁরা এ সুরের নাম দিয়েছেন ভাটিয়ালি। এখনো এই রাগিণী উত্তর ভারতীয় সংগীতে প্রচলিত আছে– যদিও তার দুটি রূপ আছে– একটি অনেকটা বাউল সুরের মতো; অন্যটি লোকসুরের আভাস দিলেও, বাংলাদেশের ভাটিয়ালির সঙ্গে তার কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। বঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলে তখন আর কোন কোন ধরনের লোকসংগীত প্রচলিত ছিলো, জানা যায় না। তবে, আগেই বলেছি, বঙ্গালি ও ভাটিয়ালি নামের মধ্য দিয়ে বঙ্গদেশে প্রচলিত দুটি সুরের আভাস অন্তত পাওয়া যায়। লোকগীতি ও জনপ্রিয় গান নিয়ে আলোচনা করবো পরের এক কিস্তিতে।
সূত্র : বিডিনিউজ